শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ (বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) গুণের বিকাশ ঘটানো। মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের আচরণ অনুশীলন করে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি আবিষ্কার করা। উভয় বিষয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব
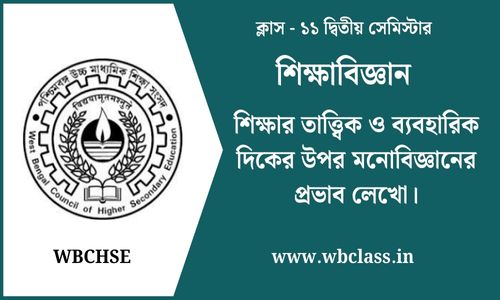
শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব
শিক্ষার যেসকল তাত্ত্বিক দিক বর্তমান তার উপর মনোবিজ্ঞানের নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-
শিক্ষার লক্ষ্য: আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করা। তাই বর্তমানে শিশুকে শেখাতে হলে দরকার শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েরই জ্ঞান। তাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে Adam এর মত হল – “The teacher teaches John latin” কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শিক্ষককে যেমন ল্যাটিন অর্থাৎ বিষয়কে জানতে হবে ঠিক তেমনি জানতে হবে John অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে।
শিক্ষার উদ্দেশ্য: শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ (বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) গুণের বিকাশ ঘটানো। মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের আচরণ অনুশীলন করে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি আবিষ্কার করা। উভয় বিষয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
পাঠক্রম: আধুনিক শিক্ষায় পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে হলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা, বয়স ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। আবার শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের উপযোগী অর্থাৎ পাঠক্রম কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এই বহুমুখী পাঠক্রমের ধারণার জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দিক যেমন বুদ্ধি, আগ্রহ, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীর মধ্যে গঠন করা দরকার। তাই শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি গভীর।
শিক্ষাদান পদ্ধতি: প্রাচীনকালে শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক যেখানে শিক্ষক ছিলেন বক্তা আর শিক্ষার্থীরা ছিল শ্রোতা। বর্তমানের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষক কেবলমাত্র সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকবেন। শিক্ষাদানের জন্য মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন প্রোজেক্ট পদ্ধতি, সমস্যাসমাধান পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি, প্রোগ্রাম শিখন পদ্ধতি, কম্পিউটার সহযোগী শিখন এবং বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদান পদ্ধতি। সুতরাং শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে অবশ্যই মনোবিজ্ঞাননির্ভর। শিক্ষকের পদ্ধতি বিষয়ক তাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার।
মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রাচীন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা ও মুখস্থ নির্ভরতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। বর্তমানে মনোবৈজ্ঞানিক দিক বিশ্লেষণ করে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নকরণ, নম্বরদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদির সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে উন্নতমানের গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু হয়েছে। আবার বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও অন্যান্য দিকের বিকাশের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয় জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: প্রাচীনকালের শিক্ষক ও আধুনিক শিক্ষকের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। এর জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। প্রাচীনকালে শিক্ষক ছিলেন বক্তা এবং তাঁর বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের শুনতে হত কিন্তু বর্তমানে সক্রিয়তাভিত্তিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষক হবেন পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী; অপরপক্ষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখবে।
বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়: শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিদ্যালয় বা শিক্ষালয়। মনোবিজ্ঞানে বলা হয় বিদ্যালয় হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়কে সম্পর্কিত করতে না পারলে শিশুর যথাযথ শিক্ষা সম্ভব নয়। সামাজিক পরিবেশ উন্নতকরণের জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রথাযুক্ত, প্রথাবহির্ভূত, প্রথামুক্ত, দূরশিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ধারণা এসেছে।
মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায় মনোবিজ্ঞান থেকে। সুস্থভাবে শিক্ষার জন্য দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের (বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে) মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ লক্ষ করা যায়। এই ধরনের আচরণ দূরীকরণের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি: শ্রেণিকক্ষে যতজন শিক্ষার্থী থাকে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠদানের চেষ্টা করবেন এবং এমন পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিষয়টি বুঝতে পারে। যেসব শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে না তাদের জন্য সংশোধনীমূলক শিক্ষণ বা Remedial Teaching-এর ব্যবস্থা করবেন।
ইতিবাচক মনোভাব: শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের দৈনন্দিন কর্মসূচি, পাঠক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠগ্রহণে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করবেন। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ভালো হয় এবং বিদ্যালয়ের প্রতি সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। ইতিবাচক মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক দিক।
দলবদ্ধতার উপলব্ধি : শিক্ষালয় হল সমাজের অংশ। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতির শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে পাঠগ্রহণ করে। বিদ্যালয় থেকে তাদের সামাজিকীকরণ হয়। বিদ্যালয় থেকে তারা দলবদ্ধভাবে থাকার শিক্ষা মনোবিজ্ঞান থেকে পায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য: শিশু জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রতিটি স্তরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি মনোবিজ্ঞানসম্মত। প্রতিটি স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি স্তরের বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের আচরণধারার কিছু না কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষকরা অবগত হবেন এবং প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীদের যাতে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকাশ সম্ভব হয় সেদিকে নজর দেবেন।
শিক্ষার ব্যাবহারিক দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব
শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা: শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পূর্বে প্রচলিত ছিল শিক্ষার্থীদের কঠোর শাসন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধাচারণ করে। তাই মনোবৈজ্ঞানিক নীতি ব্যবহার করে শিক্ষায় মুক্ত শৃঙ্খলার ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে।
শিক্ষা সহায়ক উপকরণ: শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে দর্শন নির্ভর, শ্রুতি নির্ভর, দর্শন ও শ্রুতি উভয় নির্ভর উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কোন্ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করলে ভালো হবে তা নির্ধারণ করা হয়। আগ্রহ, মনোযোগ, মনোভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি মনোবিজ্ঞানের বিষয়। মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার শিক্ষা সহায়ক উপকরণ নির্বাচনে সাহায্য করে।
সময়তালিকা: বিদ্যালয় তথা যে-কোনো শিক্ষালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সময় তালিকা গুরুত্বপূর্ণ। সময় তালিকাকে বিদ্যালয়ের ‘দ্বিতীয় ঘড়ি’ বলে। সময় তালিকা তৈরিতে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতিকে কাজে লাগানো হয়।
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি: গান, নাচ, খেলাধুলা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিকে কাজে লাগিয়ে কোনো শিক্ষার্থীদের কোন্ বিষয়ের প্রতি কীরূপ মনোভাব রয়েছে বা কোন্ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা দরকার।
আচরণগত সমস্যা সমাধান: শিক্ষার্থীদের মধ্যে (বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে) বিভিন্ন ধরনের আচরণমূলক সমস্যা দেখা যায়। এই আচরণমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোবিজ্ঞানসম্মত কৌশল রয়েছে। সেগুলিকে শিক্ষকগণ যদি যথাযথ ব্যবহার করেন তবে অনেক অপসংগতিমূলক আচরণ দূর করা যায়।
শিক্ষাগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান: কোনো শিক্ষার্থী কোন্ বিষয়ে পাঠগ্রহণ করলে সে সাফল্যলাভ করবে তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাদানই হল শিক্ষাগত নির্দেশনা। এই নির্দেশনা দেওয়ার জন্য শিক্ষকের এই বিষয়ে উপযুক্ত মনোবিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদান একজন শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনে পথ দেখাতে পারে।
বৃত্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান: বৃত্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক মনোবিজ্ঞানসম্মত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিচারবিশ্লেষণ করে উপযুক্ত বৃত্তিগত নির্দেশনা ও পরামর্শদান করতে পারেন।
ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা: পিছিয়ে পড়া, প্রতিবন্ধী ও প্রতিভাবান শিশুরা ব্যতিক্রমী শিশুদের মধ্যে পড়ে। মনোবিজ্ঞানকে যথাযথ ব্যবহার করে এই ধরনের শিশুদের শনাক্ত করে, তাদের প্রয়োজনমতো শিক্ষা পরিকল্পনা, পাঠক্রম, সময়তালিকা তৈরি করে পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করলে ব্যতিক্রমী শিশুরা উপকৃত হবে। এইভাবে অনেক ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়েও আনা সম্ভব।
সৃজনশীল শিশু চিহ্নিতকরণ: শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করতে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ করা যায়।
প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা: বর্তমানে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণে কেবলমাত্র প্রথাযুক্ত শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যেমন দূরশিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। এই ধরনের শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম, সময়তালিকা তৈরি, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদির জন্য মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়।
পাঠ পরিকল্পনা বা শিখন নকশা: বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনার পরিবর্তিত রূপ শিখন নকশা তৈরিতে ব্লুমের ট্যাক্সনমি ব্যবহার করা হচ্ছে যা মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে।
শ্রেণি ব্যবস্থাপনা: শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল— শ্রেণি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও মনোযোগ সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও দলগত শিখন, শিক্ষকের নিরপেক্ষতা ইত্যাদি। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সব ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতিকে কার্যকরী করা দরকার। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হলেই শিক্ষার মানও উন্নত করা সম্ভব হয়।
পাঠ্যপুস্তক রচনা: পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে। পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়স, চাহিদা, মানসিক বিকাশ, আগ্রহ ইত্যাদি দেখা হয়, যা জানতে মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে।
বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা: বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিদ্যালয়ের মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার। মানবসম্পদ হল শিক্ষকগণ, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক প্রমুখ। আবার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্ককে সুস্থ রূপ দিতে হলে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার। আবার সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানসম্মত সময়তালিকা, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, বিদ্যালয় পরিবেশ ইত্যাদি। সুতরাং সুষ্ঠু বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ কার্যকরী করা দরকার।
শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি: শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মনোবিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেই চলবে না এগুলির যথাযথ ব্যবহারের জন্য চাই মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাবহারিক জ্ঞান। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের কৌশলগুলিকে মনোবৈজ্ঞানের পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে।
গবেষণা: শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হলে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করা উচিত। বর্তমানে এই ধরনের গবেষণা করা হচ্ছে। এই গবেষণার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাই শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষাবিজ্ঞানকে উন্নততর করে তুলছে।
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি গভীর, শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিককে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করে তুলতে হলে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের প্রয়োগে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা উপলব্ধি ও তার সমাধানের পথ নির্ণয় করে সেগুলিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।
| আরও পড়ুন | Link |
| বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনা পর্ব ১ | Click Here |
| বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনা পর্ব ২ | Click Here |
| বৃদ্ধি ও বিকাশের অর্থ প্রশ্ন উত্তর | Click Here |